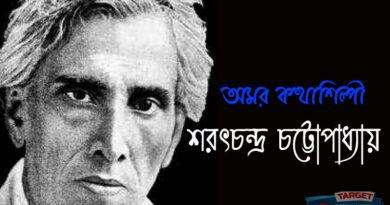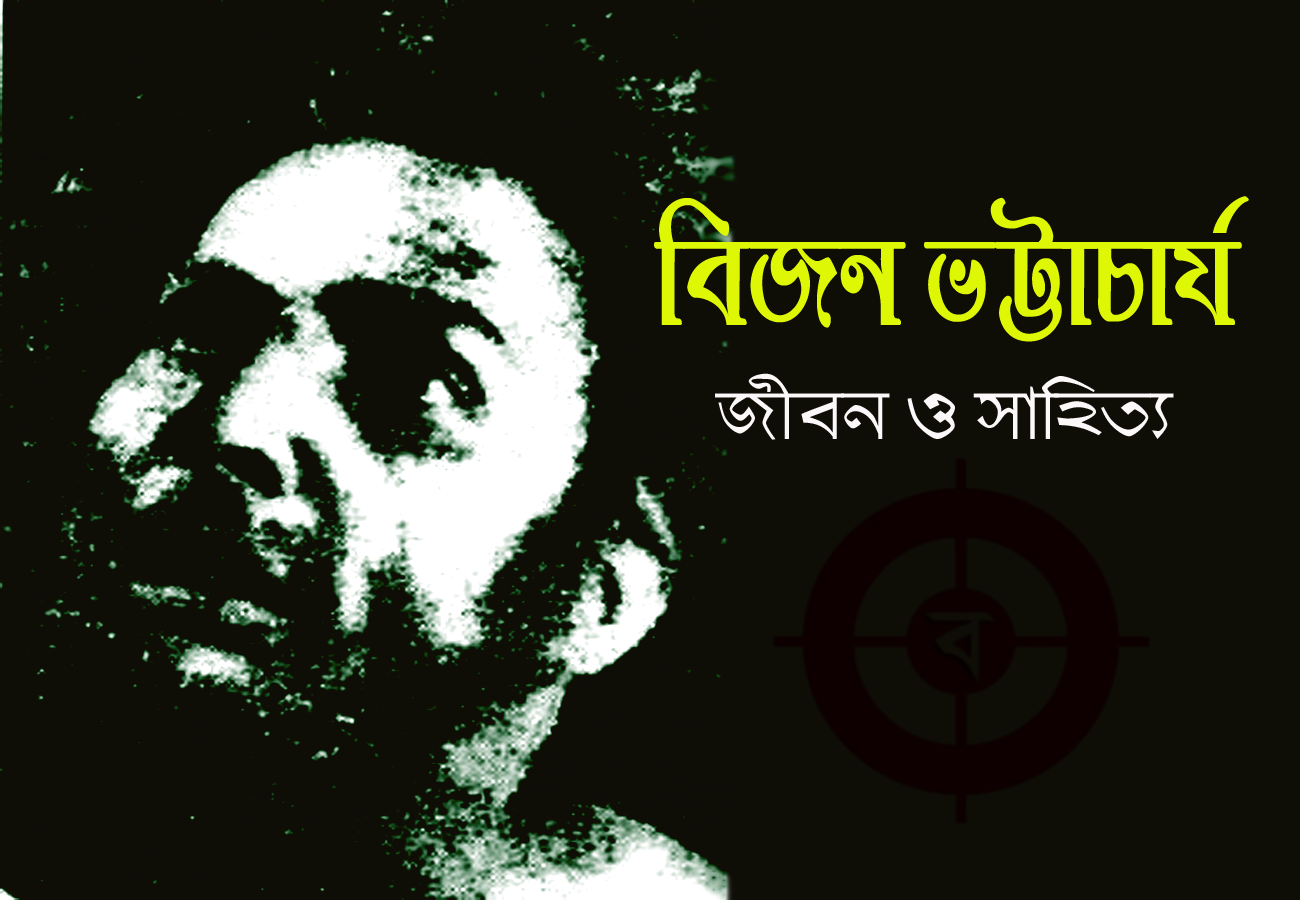মহাশ্বেতা দেবী – একটি আলোচনা
মহাশ্বেতা দেবী একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তিনি বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের বহুমাত্রিকতা ও দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি ইতিহাস থেকে, রাজনীতি থেকে যে-সাহিত্য রচনা শুরু করেন, তা শোষিতের আখ্যান নয় বরং স্বদেশীয় প্রতিবাদী চরিত্রের সন্নিবেশ বলা যায়। তিনি আজীবন সংগ্রামী চিন্তা চর্চা করেছেন এবং দেশ ও মানুষ সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হবে সেই লক্ষ্যে সাহিত্য রচনা করে গেছেন।
জন্ম ও বংশ পরিচয়
প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী ১৯২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মনীশ ঘটক ছিলেন ‘যুবনাশ্ম’ ছদ্মনাম ব্যবহারকারী কল্লোল যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং তাঁর কাকা ছিলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক। প্রখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর বিবাহ হয়।
শিক্ষাজীবন
মহাশ্বেতা দেবী রাজশাহীতে শিক্ষা শুরু করেন।পরবর্তীকালে কলকাতার আশুতোষ কলেজ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করেন।১৯৩৬ সালে তিনি পড়াশোনা করতে শান্তিনিকেতনে যান। এ-সময় মাত্র দুই বছর শান্তিনিকেতনে কাটালেও তা ছিল তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়। তখনই তাঁর লেখালেখির শুরু। ১৯৩৯ সালে তিনি যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন, তখন খগেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত “রংমশাল” পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর রবীন্দ্রনাথ -সম্পর্কিত রচনা ‘ছেলেবেলা’।
১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন, সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ১৯৪২ সালে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৩-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় মহাশ্বেতা দেবী প্রথম বর্ষে পড়েন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠন ‘Girls Student Association’ এবং দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৪ সালে মহাশ্বেতা ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে, বিএ পড়তে। ১৯৪৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে এমএ ভর্তি হন। কিন্তু তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পড়াশোনা ব্যাহত হয়।
কর্মজীবন
এম এ পাশ করার আগে মহাশ্বেতা দেবী শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন।তিনি সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে সচিত্র ভারত পত্রিকায় ফিচার এবং গল্প লেখা শুরু করেন। যদিও ১৯৪৯ সালে ইনকাম ট্যাক্সে কেরানির চাকরি পান, কিন্তু সে-চাকরি তাঁর করা হয় না। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে পোস্টাল অডিটে আপার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি নেন। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক সন্দেহে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন, পরবর্তীকালে পুনর্বার চাকরিতে বহাল হলেও তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরকারি চাকরিতে ফেরেননি।দীর্ঘ পড়াশোনা বিরতির পর ১৯৬৩ সালে তিনি প্রাইভেটে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেছেন এবং ১৯৬৪ সালে তিনি ইংরেজি অধ্যাপনায় প্রবেশ করেন। বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে। ইতিমধ্যে তাঁর প্রথম বই ঝাঁসীর রানী (১৯৫৬) সালে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে তিনি লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
সাহিত্যকর্ম
মহাশ্বেতা দেবী একজন সাংবাদিক এবং লেখিকা হিসাবে কাজ করেন। পরবর্তী কালে তিনি বিখ্যাত হন মূলত পশ্চিমবাংলার আদিবাসী এবং নারীদের ওপর তাঁর কাজের জন্য। তিনি বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন আদিবাসী ও মেয়েদের উপর শোষণ এবং বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন।ইতিহাস তাঁর সাহিত্যজীবনে সব সময়ই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। তিনি মনে করতেন, ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একইসঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে সমাজনীতি ও অর্থনীতি, যার মানেই হলো লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা। তাঁর প্রথমদিকের সাহিত্যকর্মে এই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।
আরও দেখুন
তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় খুদাবক্স ও মোতির প্রেমের কাহিনি নিয়ে ১৯৫৬ সালে নটী উপন্যাসটি লেখেন। এছাড়া প্রথম পর্যায়ে তিনি লোকায়ত নৃত্য-সংগীতশিল্পীদের নিয়ে লিখেছেন মধুরে মধুর (১৯৫৮), সার্কাসের শিল্পীদের বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে লেখেন প্রেমতারা (১৯৫৯)। এছাড়া যমুনা কী তীর (১৯৫৮), তিমির লগন (১৯৫৯), রূপরাখা (১৯৬০), বায়োস্কোপের বাক্স (১৯৬৪) প্রভৃতি উপন্যাস। মহাশ্বেতা দেবী নিজের লেখা সম্পর্কে নিজেই সমালোচক হয়ে উঠেছেন কখনো কখনো, ইতিহাস চর্চা আর সমাজ সচেতনতায় দৃঢ় হয়ে ওঠেন বলেই যেন তাঁর প্রথম পর্বের দুটো উপন্যাস তিমির লগন ও রূপরাখাতে ব্যক্তির সুখ-দুঃখ যখন কোনো সামাজিক তাৎপর্য বহন করে না বলে মনে করেছেন, তখন তিনি এ-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন – ওই বই দুটো আর ছাপবেন না। আবার অন্যদিকে গভীর সামাজিক তাৎপর্য থাকার জন্য, প্রথম প্রকাশের কুড়ি বছর পরেও ‘বিষয়বস্তুর চিরকালীনতা ও প্রয়োজনীয়তা আজও’ রয়েছে বলে মহাশ্বেতা দেবী মনে করেন, মধুরে মধুর…আজকের পাঠকের কাছে বইটি থাকা দরকার। ‘দু-অর্থে। আমার লেখার বিবর্তনের সাক্ষ্যে এবং ব্যক্তি সংগ্রামের যাথার্থ্যে।’
আরও পড়ুন
১৯৬২ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। সংসার ভেঙে গেলেও ছেলের জন্য খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সে-সময় তিনি অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন, চিকিৎসকদের চেষ্টায় বেঁচে যান। হাজার চুরাশির মা উপন্যাসে তিনি ছেলে থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন বলে জানান। এরপর তিনি অসিত গুপ্তকে বিয়ে করেন ১৯৬৫ সালে, কিন্তু সেই সংসারও ১৯৭৬ সালে ভেঙে যায়। নিঃস্বঙ্গ জীবন, বিচ্ছেদ-বিরহ-বেদনায় তিনি নিজেকে সঁপে দেন লেখা এবং শিক্ষার ব্রতে। তাঁর পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকর্মেও যে পরিবর্তন এসেছিল, এ-প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী জীবন ও দর্শন নিয়ে কল্যাণ মৈত্রের সঙ্গে আলাপচারিতায় সেই সন্ধিক্ষণকে কাটিয়ে ওঠা প্রসঙ্গে বলেন –
‘… স্রেফ লিখে। হাজার চুরাশির মা লিখেছিলাম ওই সময়েই। উপন্যাসটা পড়লে বোঝা যাবে। আর ওই সময় আমি অসম্ভব ঘুরে বেড়াতে লাগলাম – তার একমাত্র কারণ ছিল এটাই। মনের একটা কষ্টকে চাপতে চেষ্টা করছি। হয়তো এটাই আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট। ওই সময় দিনে চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা কাজ করেছি।… এদিকে আমি কোয়ালিটি রাইটিংয়ের দিকে মন দিলাম, অন্যদিকে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করলাম। এই দিকটা অবশ্যই আমার লেখাকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করেছিল। একটা না দেখা ওয়ার্ল্ড, কেউ জানে না, বোঝে না। তার সমস্ত অনুভূতিগুলি ক্ষোভ- দুঃখগুলি আমার লেখার সঙ্গে খুব মিশে যাচ্ছিল।’
এভাবেই যেন মহাশ্বেতা দেবী স্বপ্রকৃতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে ঢাকায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে আলাপে –
‘আমার প্রথম বই প্রকাশিত হয় ঝাঁসীর রানী ১৯৫৬ সালে। বইটি লিখে আমি টাকা পেয়েছিলাম। সেই থেকে আমি প্রফেশনাল লেখাতে বিশ্বাসী। লেখা আমার প্রফেশন, আমার আর কোনো জীবিকা নেই। মাঝখানে ক’বছর কলেজে পড়িয়েছিলাম, সতেরো শ’ টাকা মাইনে হতো, মনে হলো যে মহাপাপ করেছি, তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলাম। আমি যেন নিজের গুরুত্ব ভুলে যাচ্ছি। আসলে লেখাই আমার জীবিকা ছিল। আমি বিশ্বাস করি, খুব কমিটেড, খুব অল্প লোকের মধ্যে দাম থাকবে।’
এরপর তিনি ষাটের দশকের মাঝামাঝি এসে যে- উপন্যাসগুলো লেখেন, তাকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যকর্ম বলা যেতে পারে। এ-সময় তিনি আলোচিত কিছু উপন্যাস লেখেন। এগুলোর মধ্যে আঁধার মানিক (১৯৬৬), কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৬), হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪) উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে তিনি রাজনৈতিক চেতনার ও ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনী যেমন লিখেছেন, তেমনি তাঁর আদিবাসীকেন্দ্রিক উপন্যাসের সূচনাও ঘরে এ সময়।
আরও পড়ুন
হাজার চুরাশির মা এ-সময়ে লেখা তাঁর সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস ।উপন্যাসসাহিত্যে রাজনীতি এসেছে পূর্ণ অবয়বে,যেখানে তিনি রাজনৈতিক অন্ধকার দিকগুলোকে ও উপন্যাসের শৈলীতে নিয়ে এসেছেন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাস হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪)। এই উপন্যাসকে তাঁর সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনের সূচনা বলে মনে করা হয়। এ-সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-সাহিত্য ও দর্শনের নতুন সত্তার প্রকাশ ঘটে। ঘরে ফেরা (১৯৭৯) উপন্যাসেও রাজনৈতিক অন্তঃবিশ্লেষণের ভিন্ন প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ-সময় তিনি ছোটগল্পেও এই ভাবধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবী মনে করেন, সাহিত্য শুধু হৃদয়গ্রাহ্যতা নয়, মস্তিষ্কগ্রাহ্যতাও চাই। তিনি আরো জানান, পাঠক-সমালোচককে আজ এ-কথা বুঝতে হবে যে আমি যা-যা লিখেছি তার মধ্য দিয়ে এটাই বলতে চেয়েছি যে, যা-যা ঘটেছে তা শুধু আজই ঘটছে না, চিরকালই ঘটে আসছে।, তাঁর মতে, লেখকের কাজ হলো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ঘটনাবলিকে স্থাপন করা। তিনি প্রায়শ একথাও বলে থাকেন যে, তিনি ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ। মহাশ্বেতা দেবী দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিয়েছেন যে জনমানুষের সঙ্গে, তাদের বড় একটি অংশ হলো আমাদের প্রান্তিক দলিত জনগোষ্ঠীর গোত্রভুক্ত।
আরও পড়ুন
সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যকে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিবাদী আখ্যান থেকে আরো গভীরে নিয়ে গেলেন,আর বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন একেবারে সভ্য সমাজের মানুষের বিচরণের বাইরের জগৎ। ইতিহাস অনুসন্ধানে তিনি চলে গেলেন একেবারে প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে। ইতিহাস, রাজনীতি ও উপকথাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রান্তিক আদিবাসীদের জীবনসংগ্রামের কথ্য ইতিহাসকে নিয়ে এলেন সুসভ্য নাগরিকদের পাঠ্যে। তাঁর এই মানসদৃষ্টি নিছক সমাজতাত্ত্বিক নয়, বরং সমাজ মনস্তাত্ত্বিকের। তাঁর সাহিত্যের প্রেক্ষাপটেও এই বিশ্লেষিত দৃষ্টির প্রতিফলন হয়। ব্রাত্যজনের দলিত হবার ইতিহাসকে সুরক্ষার সংগ্রামে ব্যপ্ত হয়ে ওঠেন মহাশ্বেতা দেবী।
অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে ঘুরে ফেরা জীবন ও ঐতিহ্য থেকে সেই জাতিসত্তার যে ইতিহাস তিনি রচনা করেন, যা তাঁর সাহিত্য জীবনের তৃতীয় পর্ব বলা যায়। এ-সময় তাঁর লেখায় সাব-অলটার্ন ভাবধারার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। মহাশ্বেতা অন্ত্যজ আদিবাসীদের চোখ দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করেন। তাদের পুরাণকথার ভেতর দিয়ে ইতিহাস তুলে আনেন, তা ছিল আধিপত্য বিস্তারকারী হেজিমনি (hegemonic) শ্রেণির নয়, বরং শোষিত দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে তুলে এনেছেন মূলস্রোতের মানুষের সাহিত্যে। যা নিচের দিক থেকে ইতিহাসকে দেখবার ইঙ্গিত বহন করে, ওপরের দিক থেকে নয়। যা সাব-অলটার্ন স্টাডিজের অংশ হয়ে দেখা দেয়। মার্কসবাদে সাব-অলটার্ন শব্দটির ব্যবহার পুরনো। আন্তেনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত কারাগারের নোটবুক বইটিতে এ-সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেন। গ্রামশির মতে, কৃষকদের পক্ষে কলম ধরতে হবে বুদ্ধিজীবীদের।
রচনা বৈশিষ্ট্য
মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক, ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তনের ধারায় সে- দেশীয় আদিবাসী জীবনের পরিবর্তনকে বর্ণনা করেন। পাহাড়ি অরণ্য জীবনের সঙ্গে ফুটে ওঠে পরিবেশের বিপন্নতার চিত্র, যা আজকের পৃথিবীকেও বিচলিত করে, সেই আখ্যান সাহিত্যে রূপ দিয়ে আদিবাসী জীবনে ঘটে যাওয়া উলগুলান (১৯০০), কোলহান (১৮৩৫) এবং হুলকে (১৮৫৫-৫৬) নিয়ে আসেন। একের পর এক আদিবাসীদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন তিনি। তাঁর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর হলো : কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৫), চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর (১৯৮০), সুরজ গাগরাই (১৯৮৩), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), ক্ষুধা (১৯৯২) এবং কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪) প্রভৃতি। উল্লিখিত উপন্যাসগুলো ছাড়াও আরো বেশ কিছু উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী প্রসঙ্গ এনেছেন, তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে। এছাড়া তিনি আদিবাসীদের নিয়ে প্রচুর ছোটগল্পও লিখেছেন, গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য – শালগিরার ডাকে (১৯৮২), ইটের পরে ইট (১৯৮২), হরিরাম মাহাতো (১৯৮২), সিধু কানুর ডাকে (১৯৮৫) প্রভৃতি।
আরও পড়ুন
এই সব গল্প- উপন্যাসে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে যেমন আদিবাসী প্রতিবাদী চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তেমনি এদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের প্রতি প্রতিবাদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরে তুলে ধরেছেন। সাব-অলটার্ন উত্তরাধুনিকতারই এক স্টাডিজ। সেক্ষেত্রে বলা যায়, পোস্টমডার্নিজমের ক্ষেত্রে সাব-অলটার্ন আসার আগে থেকেই মহাশ্বেতা তাঁর নিজের মতো করে সাব-অলটার্ন চর্চা করেছেন। কারণ সাব-অলটার্ন স্টাডিজ সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৮২ সালে। সাব-অলটার্ন গবেষকদের মধ্যে অন্যতম – জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ। রণজিৎ গুহর মতে, উচ্চবর্গ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যারা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রভুশাসনের অধিকারী ছিল। এদের অবস্থানকে তিনি দুই স্থান থেকে দেখেছেন। প্রথমত দেশি, দ্বিতীয়ত বিদেশি।
এরা আবার দুই ধরনের, সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে ঔপনিবেশিক অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য। বেসরকারি বলতে অভারতীয় শিল্পপতি, বণিক, অর্থ ব্যবসায়ী, খনির মালিক, নীলকুঠি, চা-কফি বাগানসহ এইসব সম্পত্তির মালিক, খ্রিষ্টান মিশনারির যাজক, পরিব্রাজক এমনকি ভারতীয় জমিদার-জোতদার শ্রেণি। অন্যদিকে এই ব্যক্তিবর্গকে বাদ দিলে যারা থাকে তাদেরই নিম্নবর্গ বলে গণ্য করেছেন রণজিৎ গুহ। তিনি নিুবর্গের ইতিহাস হিসেবে যে-ব্যাখ্যা টানেন তাতে সাঁওতালদের একটি বিখ্যাত যুদ্ধ সিধু-কান্হুর পূজার কথা উল্লেখ করেন।
আরও পড়ুন
এই তাত্ত্বিকদের আলোচনার আগেই মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে শোষক আর শাসক শ্রেণির যে-দ্বন্দ্ব এবং চরিত্র পরম্পরায় যারা উঠে এসেছে তা সাব-অলটার্ন তাত্ত্বিকদের নিুবর্গ ও উচ্চবর্গের শ্রেণিকরণের ব্যাখ্যায় স্থাপন করলে যথার্থ হবে। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে ঘটনার নাটকীয়তার চেয়ে মানব-চরিত্রের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার বেশিরভাগ প্রধান চরিত্র সেই শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষ। অরণ্যের অধিকারে বীরসা মুন্ডা,ধানী মুন্ডা, সুগানা, করমি, কোমতা, সালী ও ডোনকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর উপন্যাসটিতে চোট্টি মুন্ডা, ধানী মুন্ডা, দুখিয়া, হরমু ও পাহানসহ অসংখ্য চরিত্র মুন্ডা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।
সম্মান ও স্বীকৃতি
মহাশ্বেতা দেবী সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসাধনার জন্য বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।১৯৭৯ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটির জন্য।‘ভুবনমোহিনী দেবী পদক’, ‘নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য স্বর্ণপদক’, ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মশ্রী পদক’ পান।
এছাড়া ‘জগত্তারিণী পুরস্কার’, বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার, ‘জ্ঞানপীঠ পুরস্কার’, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- প্রদত্ত ‘লীলা পুরস্কার’ও লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে ‘ম্যাগসাইসাই’ পুরস্কার পান আদিবাসীদের মাঝে কাজ করার জন্য। ১৯৯৮ সালে সাম্মানিক ডক্টরেট রবীন্দ্রভারতী অর্জন করেন। ‘ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মাননা ২০০১’ সালে অর্জনসহ আরো অনেক পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন।
তিনি কলকাতা আকাদেমির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্তও ছিলেন। বিগত কয়েক বছর ধরে নোবেল পুরস্কারের জন্য সাহিত্যিকদের তালিকায় উঠে এসেছে মহাশ্বেতা দেবীর নাম। বাংলা সাহিত্যের এই মহীয়সী লেখিকা ২৮ শে জুলাই ২০১৬ তারিখে দুপুর ৩ টে বেজে ১৬ মিনিটে পরলোক গমন করেন।